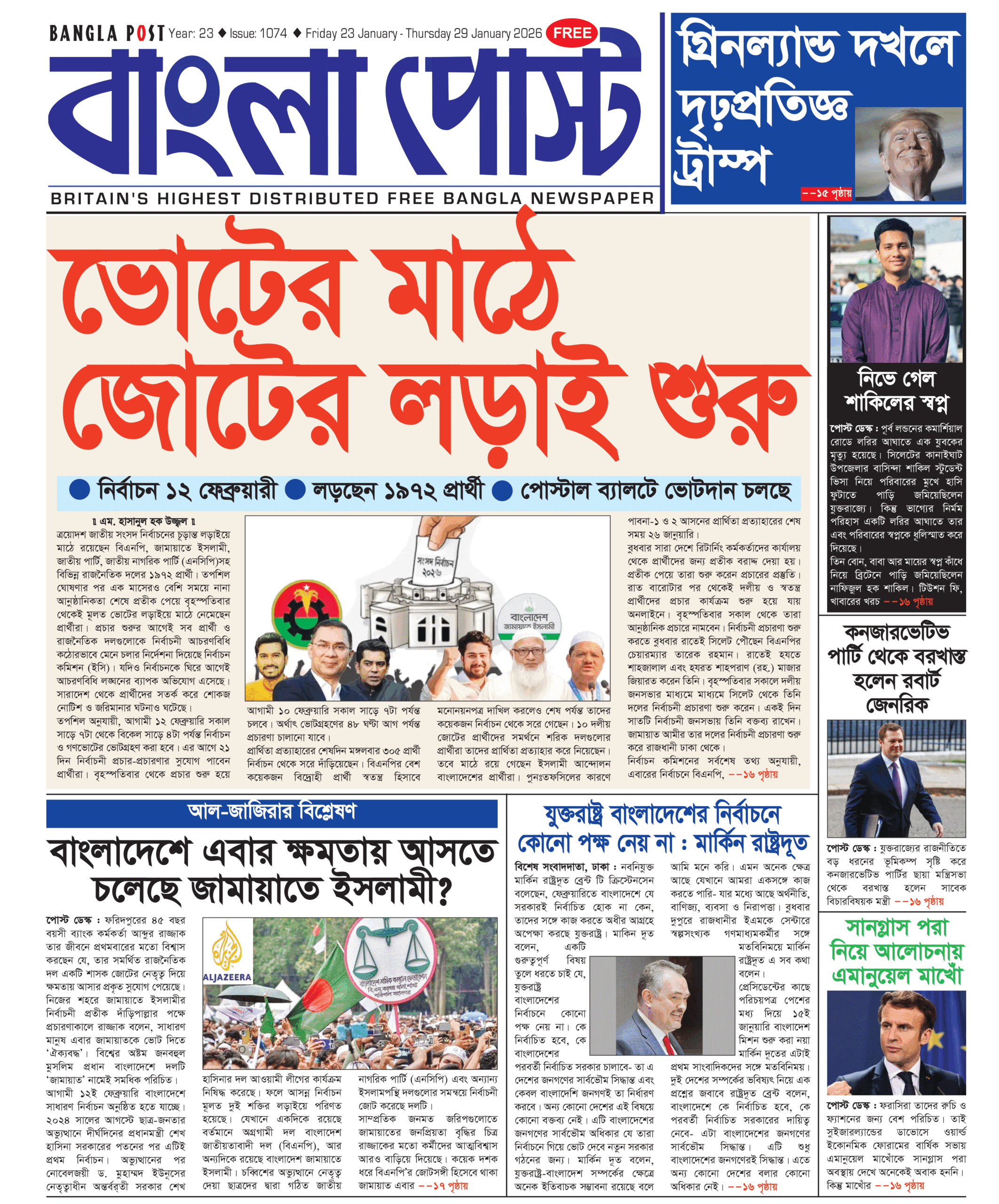গণভোট নিয়ে যত প্রশ্ন

Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD
বাংলাদেশের আসন্ন গণভোটকে কেন্দ্র ক’রে অনেকের মনেই ভীড় করেছে অজস্র প্রশ্ন। কেউ বলছেন প্রথমে সংসদে পাশ তারপর গণভোট কিনা; কেউ আবার বলছেন অধ্যাদেশের ক্ষমতা কতটুকু; কেউবা বলছেন সংবিধানের একটি শব্দ বদলাতে তো সংসদে দুই তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন; গণভোটের প্রশ্নের কাঠামো নিয়েও প্রশ্ন অনেকের; ওদিকে কেউ কেউ ভাবছেন হাঁ ভোটে কি প্রকারান্তরে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধি পাবে কিনা। তাই পাঠকদের আমি অনুরোধ করবো, রাজনীতিকে কিছুক্ষণের জন্যে পাশে রেখে এই লিখাটিকে তাঁরা যেন কিছুটা একাডেমিক আলোচনা ভেবে নেন।
গণভোটের মূল চরিত্র হলো জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ। সাধারণত কোনো দেশের সার্বভৌমত্ব, সীমানা পরিবর্তন বা সংবিধানের মৌলিক কাঠামোর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহৃত হয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে গণভোটের প্রয়োগ বিশ্লেষণ করলে আমরা বেশ কিছু বৈচিত্র্যময় উদাহরণ পাই।
২০১৬ সালে যুক্তরাজ্যের ‘ব্রেক্সিট’ (Brexit) গণভোট ছিল আধুনিক ইতিহাসের অন্যতম আলোচিত ঘটনা। সেখানে ভোটারদের সামনে একটি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট প্রশ্ন রাখা হয়েছিল: “যুক্তরাজ্য কি ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে থাকবে নাকি সদস্যপদ ত্যাগ করবে?” ভোটাররা ‘ত্যাগ করার’ পক্ষে ৫২ শতাংশ রায় দেয়। আবার ২০১৪ সালে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা নিয়ে গণভোট হয়েছিল, যেখানে প্রশ্ন ছিল, “স্কটল্যান্ড কি একটি স্বাধীন দেশ হওয়া উচিত?” জনগণ ‘না’ ভোট দিয়ে যুক্তরাজ্যের সাথে থাকার সিদ্ধান্ত নেয়। আয়ারল্যান্ডে ২০১৫ সালে সমলিঙ্গ বিবাহ বৈধ করার জন্যে সংবিধান সংশোধনের প্রশ্নে গণভোট হয়, যা সামাজিক সংস্কারে সরাসরি জনমতের এক অনন্য উদাহরণ।

যদি কোনো বিষয়ে দুইয়ের অধিক সমাধান থাকে, তবে ভোটারদের পছন্দের ক্রমানুসারে (Preference) ভোট দিতে বলা হয়ে থাকে। আবার একই দিনে আলাদা আলাদা ব্যালটে একাধিক বিষয়ের ওপরও গণভোট হতে পারে (যেমনটা সুইজারল্যান্ডে প্রায়ই ঘটে)। গণভোটের ক্ষেত্রে সুইজারল্যান্ড সবচাইতে অগ্রগামী। সেখানে নিয়মিত ব্যবধানে গণভোট হয়। যেমন: ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ, পরিবেশ নীতি বা অভিবাসন আইনের মতো সুনির্দিষ্ট বিষয়ে জনগণ সরাসরি রায় দেয়।
তাহলে বাংলাদেশে গণভোটের প্রয়োজ পড়ল কেন? ২০২৪ সালে গণঅভ্যুত্থানের পর রাষ্ট্রসংস্কার প্রস্তাব বা জুলাই সনদের মধ্যে এমন কিছু গভীর, গুরুতর এবং তাৎপর্যপূর্ণ কিছু সাংবিধানিক পরিবর্তনের বিষয় জড়িত আছে যেগুলো স্বাভাবিকভাবে বর্তমানে বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে নেই। এরকম বিশাল পরিবর্তনের বৈধতা অর্জনের জন্যে দেশের সকল স্তরের জনগণকে সম্পৃক্ত করার প্রচেষ্টা যুগে যুগে বিভিন্ন দেশের মধ্যে দেখা গিয়েছে।
জুলাই সনদকে একটি স্থায়ী ও আইনি রূপ দিতে ‘গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫’ জারি করা হয়েছে। সাধারণত সংসদ না থাকা অবস্থায় জরুরি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ৯৩(১) অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে এ ধরণের অধ্যাদেশ জারি করেন। এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সাথেই এই গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।
সাধারণত বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, সংবিধানের যেকোনো ধারা সংশোধনের জন্য সংসদে মোট সদস্য সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ (Two-thirds) ভোটের প্রয়োজন হয়। তবে ‘জুলাই জাতীয় সনদ (সংবিধান সংস্কার) বাস্তবায়ন আদেশ, ২০২৫’ এবং ‘গণভোট অধ্যাদেশ, ২০২৫’ অনুযায়ী একটি বিশেষ প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে। প্রথমে গণভোটের স্তর: গণভোটে প্রস্তাবগুলো জয়ী হতে কেবল ভোটারদের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Simple Majority) বা ৫০% এর বেশি ‘হ্যাঁ’ ভোট প্রয়োজন। তারপর সংসদের স্তর: গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হওয়ার পর, নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠিত হবে। জুলাই সনদ অনুযায়ী, এই পরিষদে সংবিধান সংস্কারের প্রস্তাবগুলো গ্রহণের জন্য পরিষদের মোট সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ (Majority) ভোটের প্রয়োজন হবে।
যদিও সংসদে ‘সংখ্যাগরিষ্ঠতা’র কথা বলা হয়েছে, অনেক আইন বিশেষজ্ঞ মনে করেন, সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী শেষ পর্যন্ত দুই-তৃতীয়াংশ সমর্থনই প্রয়োজন পড়বে। তবে যেহেতু রাজনৈতিক দলগুলো এই সনদে আগেই স্বাক্ষর করেছে, তাই সংসদে দুই তৃতীয়াংশ ভোট পাওয়াও একটি আনুষ্ঠানিকতা মাত্র হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

পরবর্তী প্রসঙ্গ হচ্ছে, জুলাই সনদের ভাষা তো আর সাংবিধানিক ভাষা নয়। এটিকে তো সাংবিধানিক রূপ দিতে হবে। সাধারণত এ কাজটি করে গণ পরিষদ । এবার যারা সংসদ সদস্য নির্বাচিত হবেন তাঁরাই ‘গণ পরিষদ’ এর কাজ করবেন, তবে এই পরিষদের নাম হবে ‘সংবিধান সংস্কার পরিষদ’। অর্থাৎ নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ দুটি টুপি পড়ে কাজ করবেন। একই ব্যক্তি সংসদ সদস্যের টুপি পড়ে সংসদের অধিবেশনে বসবেন আবার তাঁরাই সংবিধান সংস্কার পরিষদের টুপি পড়ে প্রথম ১৮০ দিন সংবিধান সংস্কারের কাজ করবেন। যদি গণভোটে ‘না’ বিজয়ী হয় তাহলে আর সংবিধান সংস্কার পরিষদ গঠনের প্রয়োজন পড়বে না। সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে যেভাবে তাঁরা কাজ করেন সেভাবেই কাজ করে যাবেন।
এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনামূলক দিক উঠে আসে। আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সাধারণত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের জন্যে আলাদা আলাদা প্রশ্ন রাখা হয়। কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে ‘জুলাই জাতীয় সনদ’-এর ভেতরে থাকা কয়েক ডজন সংস্কার প্রস্তাবকে একটি মাত্র ‘প্যাকেজ’ হিসেবে ভোটারদের সামনে পেশ করা হয়েছে। তাত্ত্বিকভাবে একে বলা হয় ‘Bundling’। বিশ্বে একই দিনে একাধিক প্রশ্নে আলাদা আলাদা ব্যালটে ভোট দেওয়ার নজির থাকলেও (যেমন সুইজারল্যান্ডে), একটিমাত্র ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ প্রশ্নের ভেতরে এতগুলো বৈচিত্র্যময় সংস্কার প্রস্তাব ঢুকিয়ে দেওয়ার নজির বিরল।
সমালোচকরা মনে করেন এই পদ্ধতিতে ভোটারদের পছন্দের স্বাধীনতা সংকুচিত হতে পারে। যেমন, একজন ভোটার হয়তো ‘প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদের সময়সীমা’ নির্ধারণে একমত, কিন্তু তিনি হয়তো ‘উচ্চকক্ষ বিশিষ্ট সংসদ’ গঠনের প্রস্তাবে দ্বিমত পোষণ করেন। কিন্তু যেহেতু প্রশ্ন একটিই, তাই তাঁকে হয় সবগুলো মেনে নিতে হবে, নয়তো সবগুলো বর্জন করতে হবে। এই ‘অল অর নাথিং’ (All or Nothing) পদ্ধতিটি সরাসরি গণতন্ত্রের আদর্শ কাঠামোর সাথে কিছুটা সাংঘর্ষিক হতে পারে বলে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন।
‘হ্যাঁ’ বিজয়ী হলে সংসদে ভোটাভুটি হবে, তবে তার চরিত্র হবে ভিন্ন। যদি জনগণ ‘হ্যাঁ’ বলে দেয়, তখন নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যদের সেই রায়কে প্রত্যাখ্যান করার কোনো নৈতিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে না। সংসদীয় ভোটাভুটি তখন একটি ‘কারিগরি সীলমোহর’ বা আনুষ্ঠানিকতায় পরিণত হবে। সংবিধান সংস্কার পরিষদ তখন প্রস্তাবগুলো বাতিল করতে পারবে না, কেবল সেগুলোকে সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য উপযুক্ত আইনি ভাষায় রূপান্তর করবে। এখানে গণভোট হলো ‘নির্দেশনা’ আর সংস্কার পরিষদ হলো ‘বাস্তবায়নকারী’।
বর্তমানে একটি রাজনৈতিক গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে, গণভোটে ‘হ্যাঁ’ জয়ী হলে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকার আরও ৬ মাস ক্ষমতায় থেকে যাবে। অধ্যাদেশ অনুযায়ী, নির্বাচনের পর গঠিত নতুন সংসদকে জুলাই জাতীয় সনদের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করার জন্য ১৮০ কার্যদিবস বা প্রায় ৬ মাস সময় দেওয়া হয়েছে মাত্র। আইনি বিশ্লেষণ বলছে, এটি ড. ইউনূস সরকারের মেয়াদ বৃদ্ধি নয়, বরং নতুন সংসদের ওপর একটি ‘সময়বদ্ধ আইনি বাধ্যবাধকতা’ মাত্র। জনগণ যদি ‘হ্যাঁ’ ভোট দেয়, তবে তারা এই সংস্কারগুলোর পক্ষে রায় দিবে, কোনো বিশেষ সরকারের মেয়াদের পক্ষে নয়। বর্তমান সংবিধান মেনেই ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন হচ্ছে এবং সেইমত বিজয়ী দলকে সরকার গঠন করার পর রাষ্ট্রপতি ৩০ দিনের মধ্যে সংসদের বৈঠক ডাকতে আহ্বান জানাবেন।
এই পুরো প্রক্রিয়াটি কি ভবিষ্যতে কোনো চ্যালেন্জের মুখে পড়তে পারে? যেহেতু এই প্রক্রিয়াটি সংবিধানের প্রথাগত ধারাকে (সংসদ আগে, গণভোট পরে) অনুসরণ না ক’রে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আগে জনগণের রায় নিচ্ছে, তাই ভবিষ্যতে এটি আইনি চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ার ঝুঁকি থেকেই যায়। কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, সংসদের দুই তৃতীয়াংশ ভোট হওয়ার আগেই কেন একটি প্যাকেজ প্রস্তাবকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হলো?
এক্ষেত্রে ‘Doctrine of Necessity’ বা বৈপ্লবিক পরিবর্তনের পর রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে গৃহীত বিশেষ পদক্ষেপের নীতিটি রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে ব’লে ধারণা করা হচ্ছে। তাছাড়া, যদি কোটি কোটি মানুষের সরাসরি রায় এই সংস্কারের পেছনে থাকে, তখন কোনো আদালত বা পরবর্তী সরকার সহজে একে অবৈধ ঘোষণা করতে পারবে বলে মনে হয়না। গণভোটে প্রাপ্ত জনগণের প্রত্যক্ষ সম্মতিই হবে এই সংস্কারের সর্বোচ্চ আইনি ও নৈতিক ঢাল।
এখানে আরো একটি আইনি জটিলতা নিয়ে অনেকে বলেন যে, বর্তমান সংবিধানে তো গণভোটের বিধানটি নেই, যা পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এখন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার কোন আইনি বলে এটি করবে? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। কিন্তু এর বিপরীতে বলা হচ্ছে,, এটি একটি অভ্যুত্থান-পরবর্তী সরকার। ডকট্রিন অফ নেসেসিটি বা প্রয়োজনীয়তার নীতি অনুযায়ী রাষ্ট্র সংস্কারের স্বার্থে তারা এই সিদ্ধান্ত নিতে পারে। সুপ্রিম কোর্ট ইতোমধ্যে এই সরকারের বৈধতা দিয়েছে। ফলে জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণে গণভোট আয়োজনে কোনো বড় আইনী বাধা থাকার কথা নয়, যদি সরকার তার রাজনৈতিক সদিচ্ছা বজায় রাখে।
গণভোটের মাধ্যমে অর্জিত এই পরিবর্তন কেবল কাগজে কলমে সংবিধানের সংস্কার নয়, বরং এটি হয়তো হবে রাষ্ট্রের সাথে জনগণের এক নতুন ‘সামাজিক চুক্তি’। যেদিকেই জনগণের রায় যাক, এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশ এক অভূতপূর্ব শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে।
……………………………………..
লেখক Dr Zaki Rezwana Anwar FRSA, MBBS, DTM&H, MS & PhD একজন চিকিৎসক, জনপ্রিয় সিনিয়র সংবাদ পাঠক, কলামিষ্ট ও আন্তর্জাতিক স্পীকার।